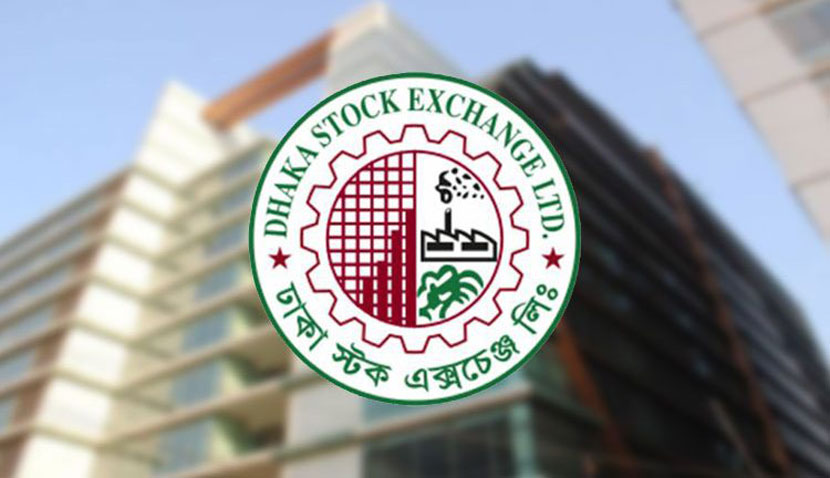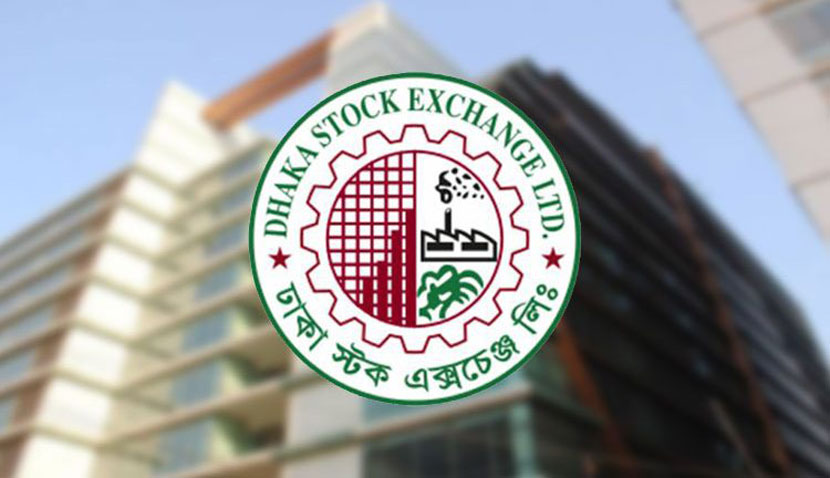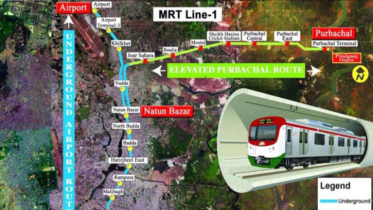ঢাকায় মেট্রোরেল শুধু পরিবহনব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খোলেনি, এর আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য নিয়েও তৈরি হয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। টিকিট বিক্রির আয় দিয়ে ঋণের কিস্তি ও বাড়তি পরিচালন ব্যয় সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প আয়ের পথ খুঁজছে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্টেশনভিত্তিক দোকান, ব্যাংকের বুথ ও বিজ্ঞাপন ভাড়া দেওয়ার। ইতিমধ্যে ৩১টি দোকান ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থাগুলো যেন যাত্রীসেবার ক্ষতি না করে, সেদিকেও সমান দৃষ্টি রাখতে হবে।
মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন এ কোম্পানির সূত্র বলছে, মেট্রোরেলের অনেক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির শর্তেই এ ব্যয়ের বিষয় রয়েছে; কিন্তু আগামী বছর থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। ফলে মেট্রোরেল পরিচালনায় ব্যয় বাড়বে। এ পরিস্থিতিতে আয় বাড়ানো না গেলে ট্রেন পরিচালনায় চাপ সৃষ্টি হবে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মেট্রোরেলে যাতায়াতের ওপর সরকার এখনো ভ্যাট মওকুফ রেখেছে। এর পরও আশপাশের দেশের তুলনায় ঢাকার মেট্রোরেলের ভাড়া বেশি। এ অবস্থায় ভাড়া বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ খুব একটা নেই। মেট্রোরেলের চলাচল বাড়ানো, স্টেশনের কাছে গাড়ি পার্কিং ও বিপণিবিতান ভাড়া দিয়ে আয় বৃদ্ধি করাটা ভালো বিকল্প।
শুরুতে আয় বাড়াতে ডিএমটিসিএল মেট্রোরেল স্থাপনার দুই স্থান বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ভাড়া দেয়। এর মধ্যে মেট্রোরেলের ভেতরে মনিটরে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। আর এর ভেতরের দেয়ালেও কিছু বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এ ছাড়া ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের মাঝখানের দরজায়ও (স্লাইড ডোর) বিজ্ঞাপন প্রচার করে আয় করছে কর্তৃপক্ষ। এরপর মেট্রোস্টেশনে ব্যাংকের বুথ ভাড়া দেওয়া হয়।
বর্তমানে মেট্রোস্টেশনে ১১টি ব্যাংকের ১৪৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। একেকটি স্টেশনে একাধিক ব্যাংকের বুথ রয়েছে। এগুলো উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ ভাড়া পায়।
এ ছাড়া চারটি স্টেশনের নিচে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে। এসব স্টেশন হচ্ছে—উত্তরা (উত্তর), আগারগাঁও, ফার্মগেট ও কমলাপুর। এসব অব্যবহৃত জায়গায় স্টেশন প্লাজা নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর আওতায় ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য পার্কিং ভাড়া দেওয়া ও দোকান বরাদ্দের কথা রয়েছে। তবে এ ধরনের ব্যবস্থার কারণে স্টেশনের নিচে যানজট হতে পারে—এমনটাও আলোচনা আছে। ফলে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ গণমাধ্যম কে বলেন, যাত্রীদের ওপর বাড়তি ভাড়া চাপানোর সুযোগ কম। এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মেট্রোরেলের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যাত্রী আয় (টিকিট বাবদ আয়) বাড়ানো। এর বাইরে দোকান ও ব্যাংকের বুথ ভাড়া দিয়ে, বিজ্ঞাপন প্রচার করে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও (খরচের) চাপ কমবে।
১৪ স্টেশনে ৩১ দোকান
আগারগাঁও ও কারওয়ান বাজার ছাড়া মেট্রোরেলের উত্তরা (উত্তর) থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মোট ১৪টি স্টেশনে ৩১টি দোকান ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ। এসব দোকান ইতিমধ্যে স্টেশনের কনকোর্স হলের ননপেইড অঞ্চলে আছে; যা লাল শাটার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ইজারা সম্পন্ন হলে ইজারাদার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দোকান সাজিয়ে নিতে হবে। এ জন্য নীতিমালা তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ।
ডিএমটিসিএল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভাড়া নিতে আগ্রহীরা ১৭ আগস্ট থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অফিস চলাকালীন মেট্রোরেল ভবনের (৩১৯ নম্বর রুম, লেভেল-৩, দিয়াবাড়ি, উত্তরা) অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিটি ফরমের মূল্য ৫ হাজার টাকা, যা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (অফেরতযোগ্য)। ইতিমধ্যে ৩০টির মতো আবেদন জমা পড়েছে।
আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া নেওয়ার জন্য কিছু মৌলিক যোগ্যতা থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ব্যাংকের ইস্যুকৃত গত এক বছরের লেনদেন বিবরণী ও আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র।
এ ছাড়া আবেদনকারীকে তাঁর ব্যবসার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। কোন পণ্য বা সেবা বিক্রি করা হবে, কীভাবে পরিচালনা করা হবে ও জনবল কাঠামো কেমন হবে—এমন বিস্তারিত তথ্য আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পরিকল্পনায় মেট্রোস্টেশনের নিরাপত্তা ও নান্দনিকতা অগ্রাধিকার পাবে।
চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। আবেদন জমার সময় বার্ষিক ভাড়ার ১৫ শতাংশ জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে। চুক্তি সইয়ের আগে বার্ষিক ভাড়ার ২০ শতাংশ নিরাপত্তা জামানত ও এক বছরের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। প্রতিবছর ভাড়া ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে, এ পর্যন্ত যেসব আবেদন জমা পড়েছে, এর বেশির ভাগই ফাস্টফুড ও কফি শপের জন্য। তবে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মেট্রোস্টেশনের দোকানে গ্যাসের চুলার অনুমোদন দেওয়া হবে না।
দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র–পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হবে। প্রয়োজনে দরদাতাদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেবে ডিএমটিসিএল। দোকানের ভাড়া কীভাবে নির্ধারিত হবে—এমন এক প্রশ্নের জবাবে ডিএমটিসিএলের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যম কে বলেন, নির্ধারিত স্টেশনের নিচের দোকানের ভাড়ার পাশাপাশি মেট্রোরেলের সুনাম যুক্ত হবে। তবেই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।
স্টেশনে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য যেসব দোকান রয়েছে, এগুলোর আয়তন ২০০ থেকে ২০০০ বর্গফুট। সর্বোচ্চ চারটি দোকান বরাদ্দ দেওয়া হবে উত্তরা উত্তর স্টেশনে। পল্লবী, কাজীপাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সচিবালয় স্টেশনে ইজারা দেওয়া হবে তিনটি করে দোকান। দুটি করে দোকান রয়েছে উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, মিরপুর-১১, শেওড়াপাড়া, বিজয় সরণি ও মতিঝিল স্টেশনে। ফার্মগেট, শাহবাগ ও মিরপুর-১০ স্টেশনে বরাদ্দ দেওয়া হবে একটি করে দোকান।
ব্যয় বেশি, ভাড়া চড়া, আয় কম
২০১২ সালে উত্তরা থেকে মিরপুর ও ফার্মগেট হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু করা হয়। ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর চালু হয় আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ।
শুরুতে মতিঝিল পর্যন্ত এ মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও পরে তা কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এখন সব মিলিয়ে প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫৯ শতাংশ অর্থ জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জাইকার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে মেট্রোরেলের আয় ও ঋণের কিস্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত অর্থবছরে টিকিট বিক্রি থেকে অনিরীক্ষিত (প্রভিশনাল) আয় ছিল ৪০০ কোটি টাকার মতো। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ আয় ছিল প্রায় ২৪৪ কোটি টাকা। ২০২২ সালে আংশিক চালুর পর ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় হয়েছিল ২২ কোটি টাকার বেশি।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, শুধু বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য খাতে গত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। আগামী বছর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের খরচ প্রকল্প থেকে বহন করা হবে না। তখন মেট্রোরেলের আয় থেকেই যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বছরে ব্যয় ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। মেট্রোরেলের স্থাপনা যত পুরোনো হবে, ব্যয়ও তত বাড়বে। লোকবলের পেছনে বেতন-ভাতাও বাড়বে।
এদিকে জাইকার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষকে। কোম্পানিটির সূত্র জানায়, মেট্রোরেলের নির্মাণকালীন ১০ বছর পর্যন্ত জাইকার ঋণের মূল কিস্তি দিতে হয়নি, যা গ্রেস পিরিয়ড হিসেবে পরিচিত। ২০২৩ সালের জুন থেকে সীমিত আকারে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৫ কোটি টাকার মতো পরিশোধ করা হয়েছে। এ বছর আরও ১০ কোটি টাকা শোধ করতে হবে
তবে আগামী বছরের মে থেকে পরিশোধ করতে হবে বড় অঙ্কের ঋণ। সব মিলিয়ে তখন থেকে পরবর্তী এক বছরে পরিশোধ করতে হবে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকার কিস্তি।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে, এরপর পর্যায়ক্রমে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরিমাণ আরও বাড়বে। ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে এমআরটি-৬ নির্মাণে নেওয়া ঋণের কিস্তি হিসেবে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ এ সময়ে গড়ে বছরে ৭৪০ কোটি টাকা ঋণের কিস্তি বাবদ পরিশোধ করতে হবে।
এ বিষয়ে পরিবহনবিশেষজ্ঞ সামছুল হক গণমাধ্যম কে বলেন, মেট্রোরেলের আয় বাড়াতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে যত দোকান পরিকল্পিত আছে, তার বেশি দেওয়া যাবে না। দোকানগুলো থেকে যাত্রী বা সাধারণ মানুষ সঠিক সেবা পেলেন কি না, বা ঠকানো হচ্ছে কি না, এগুলোও দেখতে হবে। অর্থাৎ এমনভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে যাত্রীদের অসুবিধা না হয়। আবার একজনে বরাদ্দ নিয়ে অন্যজনকে দেওয়া ও রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালনা যাতে না হয়, তা দেখতে হবে।