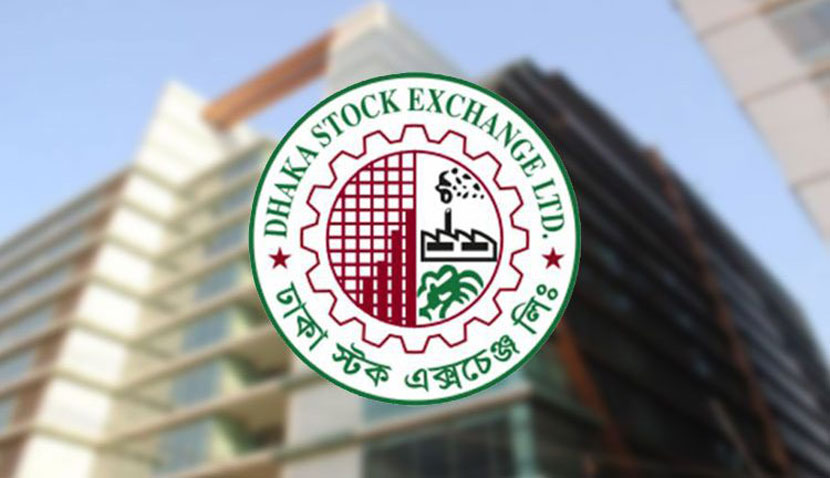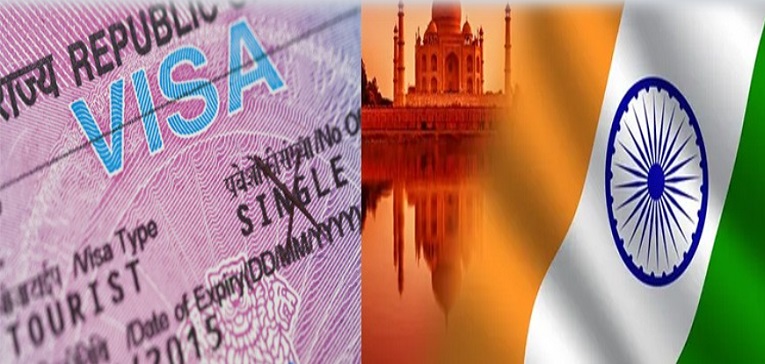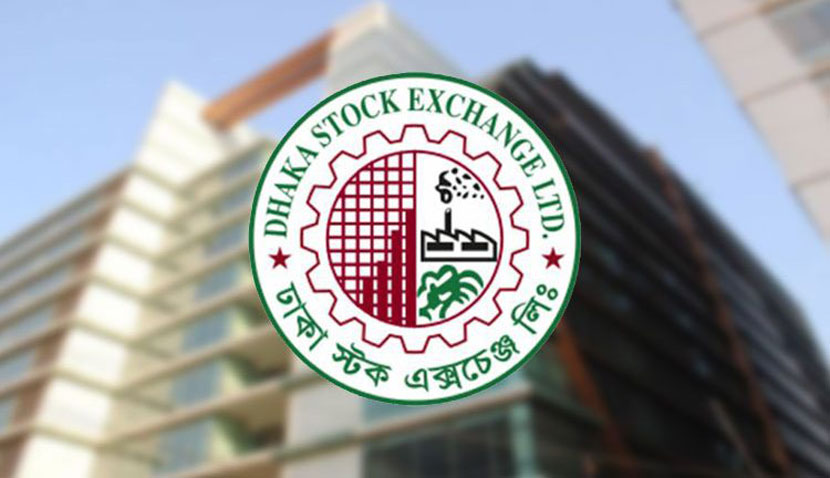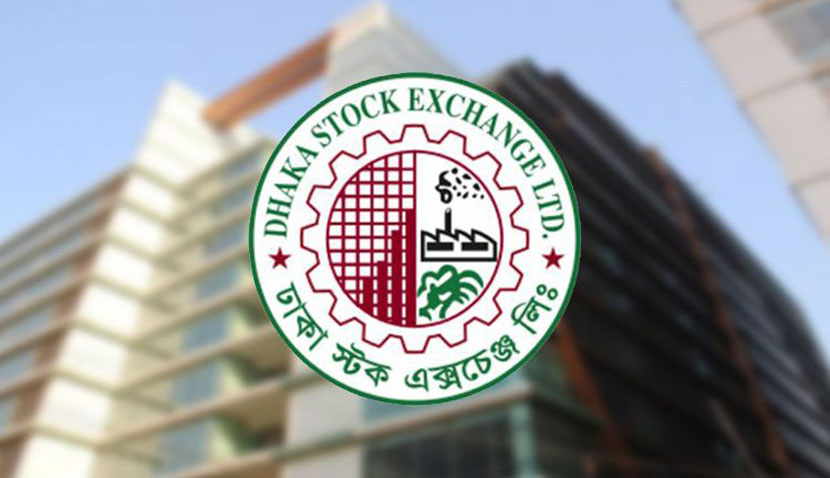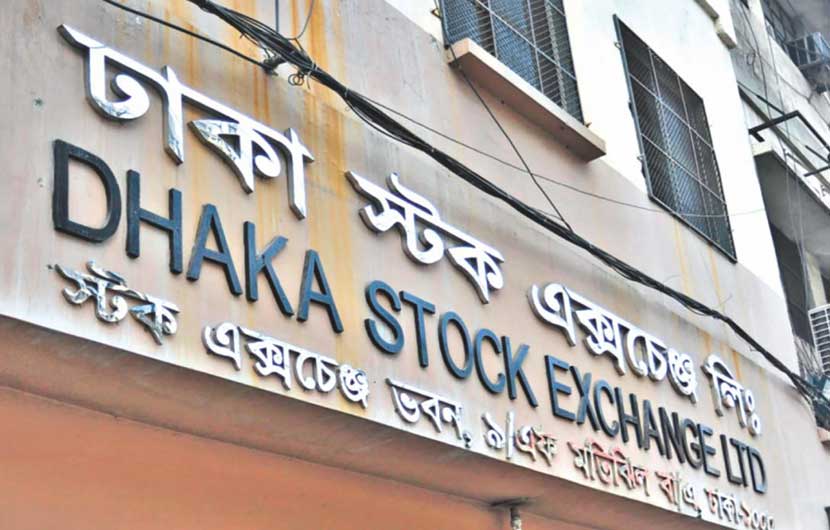সিরাজগঞ্জ—বাংলাদেশের অন্যতম বয়নকেন্দ্র, যেখানে প্রতিটি সুতোয় গাঁথা শুধু কাপড় নয়, একেকটা জীবনের গল্প। প্রকৃতির বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করেও টিকে থাকা এই শিল্প এখন শুধু দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই—ভারতের বাজারেও ছড়িয়ে পড়েছে এর খ্যাতি। বেলকুচি, শাহজাদপুর ও চৌহালীর তাঁতিরা যেমন রঙের সমাহারে শাড়িকে দিয়েছেন নতুন মাত্রা, তেমনি তৈরি করেছেন অর্থনীতির শক্ত ভিত।
একসময় পাবনার অংশ থাকলেও সিরাজগঞ্জেই শাড়ি শিল্প পেয়েছে প্রাণ। দেলুয়া, তামাই, শেরনগরের মতো গ্রামে এক সময় হাজার হাজার তাঁত বুনতো, যার ধ্বনি পৌঁছে যেত মুম্বাই বা করাচি পর্যন্ত। আজ দেলুয়া যমুনায় বিলীন হলেও তার উত্তরাধিকার বহন করছে নতুন প্রজন্ম। বেলকুচির হাটে এখন প্রতি সপ্তাহে বিক্রি হয় ৩০০ কোটি টাকার পণ্য, যার ৩০ শতাংশই যায় রপ্তানিতে—ভারতের ব্যবসায়ীরাই বড় অংশীদার।
শাড়ির বৈচিত্র্য এখানে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি প্রস্তুতপ্রণালিও জটিল ও সময়সাপেক্ষ। সুতা কিনে মার্সেলাইজিং, ডাইং, মাড়, শুকানো, টানা দেওয়া—এসব পার হয়ে তবে শুরু হয় বুনন। সাধারণ শাড়ি তৈরি হতে লাগে ছয় ঘণ্টা, জটিল ডিজাইন হলে কয়েক দিনও লাগে। কাপড়ের উপকরণেও এসেছে বৈচিত্র্য: সুতি থেকে শুরু করে খাদি, তসর, পালেক্স, পলিয়েস্টার, এমনকি জরি পর্যন্ত।
ফ্যাশন হাউস ও ডিজাইনারদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হয় কাটিং বুটা, জলবুটা, টেডি বা মনুপুরা নামের শাড়ি। রঙের ব্যবহারেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। টিভি, ফ্যাশন জগৎ এমনকি ভারতীয় ধারাবাহিকের প্রভাবও ফেলছে নকশা ও রঙে। তবে এখানে ডিজাইনারের ঘাটতি ও নীতিগত সহায়তার অভাবের কারণে বয়নশিল্পীরা অনেক সময়ই প্রাপ্য সম্মান ও প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত থাকেন।
তাঁত বোর্ডের অবহেলা, আমদানিনির্ভরতা আর পাওয়ারলুমের আগ্রাসন হস্তচালিত তাঁতকে করছে সংকটে নিপতিত। অথচ এই শিল্পে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় চার লাখ মানুষ, যাদের শ্রম দেশের অর্থনীতিতে রাখছে দৃশ্যমান ভূমিকা। সিরাজগঞ্জের শাড়ি টাঙ্গাইলকে ছাড়িয়ে রপ্তানিতে এগিয়ে গেছে বহু আগেই। এখন দরকার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য সময়োপযোগী, বাস্তবমুখী ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা।