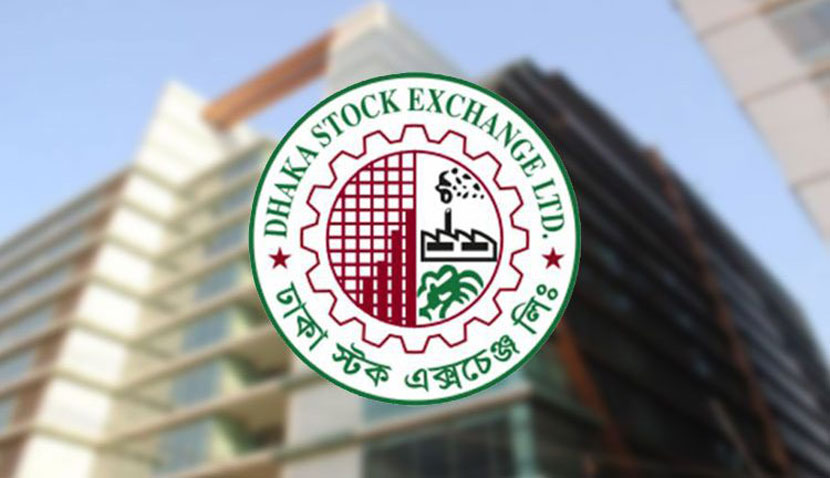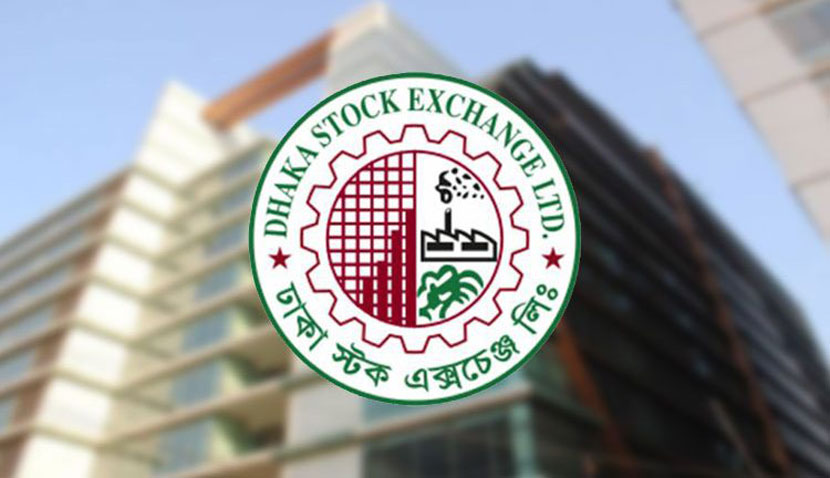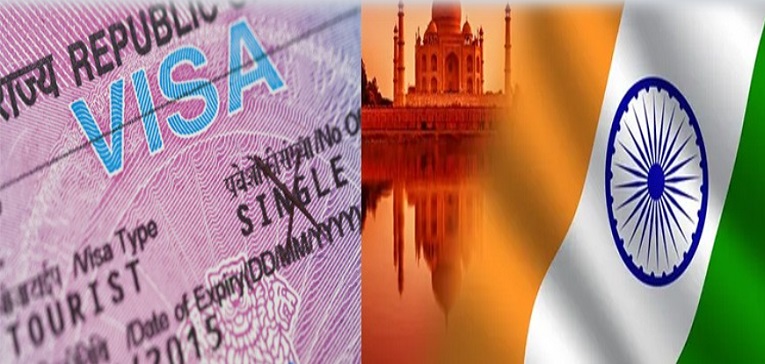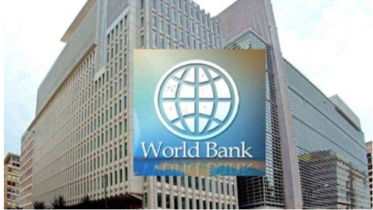বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের ক্রমবর্ধন দেশের অর্থনীতিতে ‘ক্রেডিট ক্রাঞ্চ’ তৈরি করছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) সতর্ক করেছে, এই ঋণ বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীর আস্থা কমাচ্ছে, বিনিয়োগ মন্থর করছে এবং দেশকে স্ট্যাগফ্লেশন-এর পথে নিয়ে যেতে পারে।
পিআরআই-এর “মাসিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি” প্রতিবেদন অনুযায়ী, খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬.৪৪ লাখ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশ। পিআরআই-এর প্রিন্সিপাল ইকোনমিস্ট আশিকুর রহমান বলেছেন, কমপক্ষে ১৬টি ব্যাংক নতুন ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়েছে।
গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে ‘ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট’ প্রায় ৯.৫ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে, যা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কম। পিআরআই জানান, কার্যকর খেলাপি ঋণ সমাধানের জন্য বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন, যা তত্ত্বাবধান, আইনি কাঠামো এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় নিশ্চিত করবে।
আশিকুর রহমান সতর্ক করেছেন, বড় পরিমাণ খারাপ ঋণ ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যা বিনিয়োগ ধীর করে, সরকারি ব্যয় সীমিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস করে। তিনি বলেন, "খেলাপি ঋণ এখন শুধু ব্যাংকিং ইস্যু নয়, এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা।"
বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)-এর সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তাদের সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না, বরং ব্যবসায়িক পরিবেশও সহায়ক নয়। ঋণের পুনঃপরিশোধের সময়কাল কমানোর ফলে ঋণ দ্রুত খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তিনি সুপারিশ করেন আইনশৃঙ্খলা, জ্বালানি সংকট সমাধান, চাঁদাবাজি বন্ধ এবং ব্যবসায়িক নীতি সহায়তা।
ইভেন্টে পিআরআই-এর চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার বলেন, রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট বাড়ার ফলে রফতানিকারীদের জন্য প্রতিযোগিতা কঠিন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে ডলার কিনে টাকার অবমূল্যায়ন করতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
এদিকে, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা ঋণ ব্যবস্থাপনা, করনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এ.কে.এম. আতিকুর রহমান বলেছেন, ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের প্রকৃত মাত্রা গত জুলাই বিদ্রোহের পর প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সতর্ক করেছেন, রফতানি বহুমুখীকরণ এবং ট্রাম্প যুগের শুল্ক নীতি এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ।